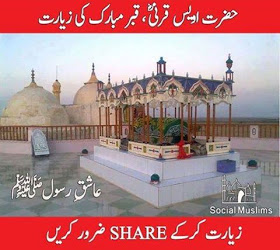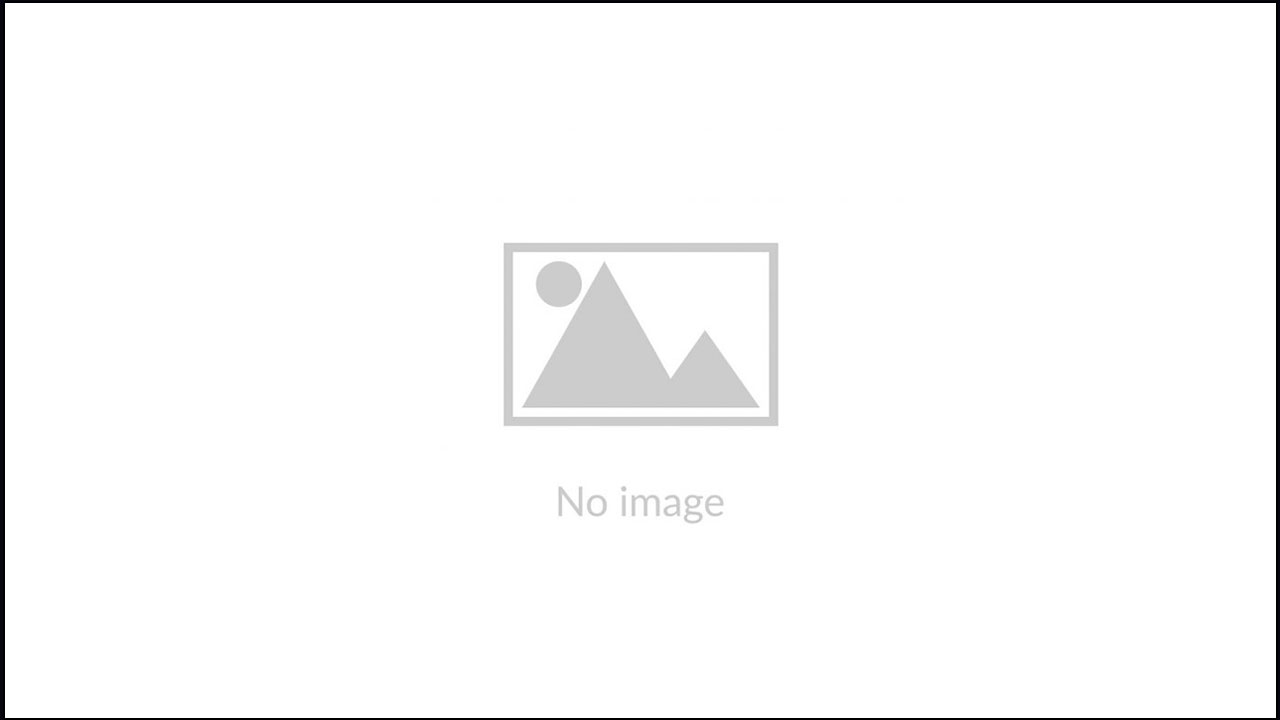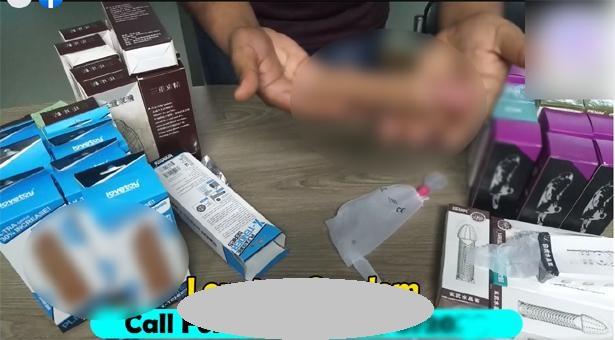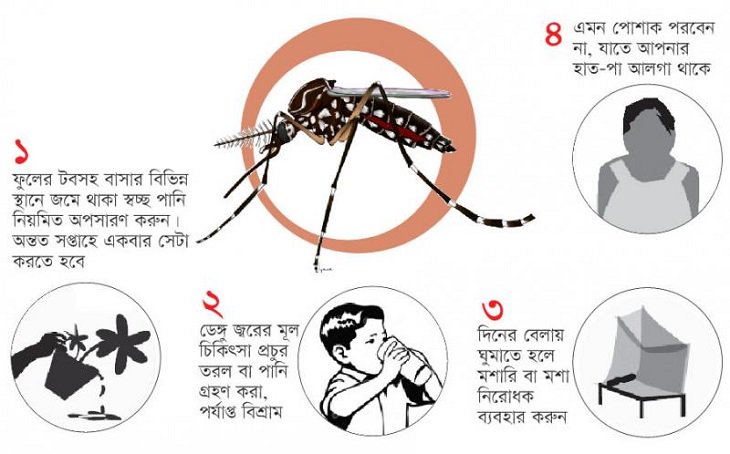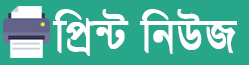
অর্থনীতি ডেস্ক: বাংলাদেশসহ ১৮৫টি দেশ ও অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে। বাংলাদেশি পণ্যে শুল্কের হার বাড়িয়ে ৩৭ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। ন্যূনতম ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ট্যারিফের কবলে পড়েছে এসব দেশ।
দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির কারণেই এমন শুল্ক আরোপ হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এই শুল্ক আরোপ বাংলাদেশের রফতানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে শঙ্কা তাদের।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো দেশকে উদ্দেশ করে যুক্তরাষ্ট্র এই শুল্ক আরোপ করেনি। দেশটির সঙ্গে যেই দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, সেসব দেশের ওপরেই এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ দেশটিতে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি এবং দেড় বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। সুতরাং এখানে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের মতো বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। ফলে নতুন শুল্ক আরোপের মধ্যে বাংলাদেশ পড়তে পারে এমন ধারণা আগে থেকেই ছিল।
সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, নতুন শুল্ক আরোপের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হলে অভ্যন্তরীণভাবে কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্প-কারখানাগুলোকে আরও কার্যকরী কীভাবে করা যায় তা চিন্তা করতে হবে। পাশাপাশি ভেল্যু চেইনকে সাবলীল করতে পরিকল্পনা করতে হবে।
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেছেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্য রফতানি করে থাকে, সেই সমধর্মী পণ্য রফতানি করা অন্যান্য দেশগুলোর ওপরেও উচ্চ শুল্ক আরোপ হয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভারত, চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়াতনাম, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা। সেক্ষেত্রে এটিকে মন্দের ভালো বলা যায়। কারণ শুধু বাংলাদেশেই নয়, অন্যান্য দেশগুলোর ওপরেও কাছাকাছি শুল্ক আরোপ হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ থেকে পণ্য নিতে দেশটির আমদানিকারকের উচ্চ মূল্য দিতে হবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের পণ্য ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। ফলে বাংলাদেশের রফতানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
রফতানি বাজার ধরে রাখতে কী ধরনের সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন? এমন প্রশ্নে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রিসিপ্রোকাল এই ট্যারিফটি একটি নতুন ধারণা। বিষয়টি এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এছাড়া, এটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অগরাগাইজশনের (ডব্লিওটিও) নীতিবিরোধী। কতদিনের জন্য এটি আরোপ করা হয়েছে বা কবে তুলে নেয়া হবে তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। এক্ষেত্রে দেশটি অন্যান্য দেশের সাথে ট্যারিফ নিয়ে কীভাবে সমঝোতা করে সেটিও দেখতে হবে। ভারত, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে দেশটির বাণিজ্য বেশি। এই দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে নেগোশিয়েট করে তা দেখে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।
দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের সাথে ব্যবসায়ীদের আলোচনা করা দরকার জানিয়ে তিনি বলেন, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তারা যাতে এমনভাবে মূল্য নির্ধারণ করে, যাতে ট্যারিফটি সমন্বয় করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ যাতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাঁধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়েও আলাপ করতে হবে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আলোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের পদক্ষেপ নজরে রেখে কৌশল নির্ধারণে একটি পর্যবেক্ষণ সেলও খুলতে হবে।
বিমসটেক সম্মেলন আঞ্চলিক বাণিজ্য বিকাশে কী ধরণের ভূমিকা রাখবে? এমন প্রশ্নের জবাবে সিপিডির এ গবেষণা পরিচালক বলেন, ২০ বছর পেরিয়ে গেলেও বিমসটেকের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এবার ২০৩০ সালের জন্য একটি রোডম্যাপ ঘোষণার কথা রয়েছে। তবে সেটিও পরিষ্কার নয়। তবে সমুদ্র পরিবহন সহযোগিতা চুক্তিটি আশা দেখাচ্ছে। তবে এফটিএ নিয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও দেশগুলো কার্যকর কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারছে না। ভারত ও থাইল্যান্ড কার্যকর রাজনৈতিক ঐকমত্যে না পৌঁছালে বিমসটেককে কার্যকর করা কঠিন হবে।
এদিকে, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোর সংস্কার নিয়ে উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোও নতুন করে চিন্তা করবে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অগরাগাইজশনের (ডব্লিওটিও) ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের আস্থা নেই। সামনের দিনগুলোতে সেটির প্রভাব দেখা যাবে। এটি নিয়ে ডব্লিওটিও’র কাছে কোনো অভিযোগ করে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।
Array